বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস: আহমদ ছফার ভাবনা ও বর্তমান

বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস: আহমদ ছফার ভাবনা ও বর্তমান
অর্ণব সান্যাল

‘বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ–কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।’
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাস নিয়ে লিখতে বসে শুরুতেই এমন মন্তব্য করেছিলেন কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং সর্বতোভাবে একজন স্বাধীন চিন্তক আহমদ ছফা। ১৯৭২ সালে তিনি লিখেছিলেন ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হওয়ার পর এ নিয়ে বইও বের হয়েছিল। এই রচনাটির ৫০ বছর পূর্তিও হয়ে গেছে। চলুন, এখন একটু পেছন ফিরে এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির আদি ধারা অবলোকন করা যাক এবং অবশ্যই তার পাশাপাশি বর্তমান ধারার একটি তুলনামূলক আলোচনাও থাকবে।
প্রশ্ন উঠতে পারে, আহমদ ছফার ৫০ বছর আগের দেওয়া বক্তব্য আমরা কি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করে নেব? যেমন আপত্তি জানানো যেতেই পারে, তেমনি ছফার বেশ কিছু বিশ্লেষণ যুক্তির বিচারে গ্রহণ করে নেওয়াই শ্রেয়। ছফা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিবৃত্তির তৎকালীন বিন্যাসকে আতশ কাঁচের নিচে নিয়েছিলেন। তাতে ক্ষুরধার সমালোচনা ছিল। হ্যাঁ পাঠক, সত্যিই সেই সমালোচনায় ধার ছিল, মরচে নয়। এবং তাতে অনেকের আঁতে ঘা লেগেছিল এবং এখনও নিশ্চিতভাবেই লাগে।
১৯৭২ সালে লেখা ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’ রচনায় আহমদ ছফা তৎকালীন বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীদের ‘পাকিস্তানি’ মানসিকতার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদ। ছফার কথায়, বাংলাদেশের উন্মেষকালে এখানকার বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর হামলা বা বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টার প্রশ্নে কিছু ‘পোশাকি’ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করার কারণে বুদ্ধিজীবীদের কাউকে চাকরি হারাতে হয়েছে বা জেলে যেতে হয়েছে—এমন কোনো মানুষের নাম জানার সৌভাগ্য হয়নি বলে দাবি করেছিলেন ছফা। তাঁর আরও অনুযোগ ছিল যে, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজের ‘অনেক গভীর, বিকট হাঁ করা’ প্রশ্নের বিষয়ে এক–দুজন ব্যতীত কোনো ‘প্রতিষ্ঠাবান’ বুদ্ধিজীবীই উচ্চবাচ্য করেননি। এসবের কারণ হিসেবে ছফা যেমন সাংস্কৃতিক এলিট শ্রেণির সুবিধাবাদী মনোভাবকে দায়ী করেছেন, তেমনি তৎকালীন শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের অপরিণত ভূমিকা এবং স্নায়ুযুদ্ধের কবলে পড়া বিশ্বের বিভিন্ন অক্ষশক্তির (যেমন: মার্কিন ডলার) হয়ে কাজ করাকেও দায়ী করেছেন। এসেছে ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও দূরদর্শিতার অভাবের দরুণ ধীরে ধীরে সংস্কৃতি এবং রাজনীতি একে–অপরের পরিপূরক না হয়ে দুটি আলাদা জলঅচল কুঠুরিতে পরিণত’ হওয়ার বিষয়টিও।

মজার বিষয় হলো, ৫০ বছর পরও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সমস্যা সেই সুবিধাবাদই। এ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর সজোরে আওয়াজ তোলেননি। যে ব্যক্তিকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে পুরো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন হলো, তাতেও খুব জোরালোভাবে একযোগে প্রতিবাদ আসেনি এ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে। হয়তো তখনকার ভয়ের আবহকে কারণ হিসেবে দেখাতে চাইবেন অনেকে, কিন্তু যেকোনো ভয়ের জাল ছিঁড়ে আত্মপ্রকাশ করাই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল কাজ। তবে হ্যাঁ, এ দেশে আনুষ্ঠানিক সামরিক শাসনামলের শেষের দিকে আমরা তার কিছুটা দেখতে পেয়েছি। সে সময় কেউ কেউ যেমন বিক্রিও হয়েছেন, অনেকেই আবার গণতন্ত্রে ফিরতে প্রতিবাদে মুখরও হয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে ফেরার পরই সেই একমুখী প্রতিবাদ, বহুমুখী সুবিধাবাদে ফের আটকে যায়। ১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের (কবি–সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী প্রমুখ) নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখেছি এবং এখনও দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব বুদ্ধিজীবীর একদম নিজের ঘরের চালে আগুন না লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা মুখ খোলেন না। এ দেশে এখন কবি–সাহিত্যিকদের চেয়েচিন্তে পুরস্কার নিতে দেখা যায়। সাংবাদিকেরা নিরপেক্ষতার ভিত্তিমূল ভেঙেচুরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের বয়ানে নিজেদের পেশাভিত্তিক সংগঠনকে দু ভাগ করে এক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বা ভেতরে আলাদা আলাদা সমাবেশ করেন। কেউ বলেন, দেশ ভালো চলছে। কেউ আবার সমালোচনা করতে গিয়ে ভালো–মন্দের বিচারক্ষমতা আর বজায় রাখেন না। এই দুই পক্ষ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মতো নিজেদের রাজনৈতিক পথের সুপ্রশংসা করে যান, তাতে যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক! আর যারা এসবে নেই, তারা কেউ কেউ করপোরেট গোলামি করছেন। কিন্তু কয়জন আর শুধু সাংবাদিকতার মূলনীতির নিরিখে সাংবাদিকতা করছেন? সংখ্যাটা বোধহয় আঙুলের কর গুণেই বের করা সম্ভব হবে। আর এসবের মূল কারণ সর্বতোভাবে সে–ই কলাটা–মুলোটা।
একই অবস্থা দেখা যাবে শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী প্রমুখদের মধ্যে। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ নীল। দলবাজি এতটাই করুণ অবস্থায় গেছে যে, ভিন্নমতের কারও ছায়াও মাড়াতে চান না কেউ, যুক্তি দিয়ে সমালোচনা তো দূরের কথা। তাদের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষভাবে শিক্ষাদানটাও করতে পারেন কিনা সন্দেহ। কীভাবে পারবেন? কেউ কেউ যে রাজনৈতিক দলের কৌশল নির্ধারণের কান্ডারির ভূমিকাও নিচ্ছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। প্রায় ৮/১০ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকু বলতে পারি যে, আজকালকার শিক্ষকদের মধ্যে কিয়দংশই মেরুদণ্ড সোজা রেখে হক কথাটা কইতে পারেন না। কেউ কেউ শ্রেণিকক্ষে ‘সেকুলারিজম’–এর সঠিক অর্থটি বলতেও ভয় পান! দু–একজন যে একদম নেই, তা নয়। কিন্তু তাদের গলায় আমরাই পরাচ্ছি জুতার মালা। ফলে হাজার হাজারের সত্যের অপলাপের বিপরীতে দু–একজনের সত্যকথন একসময় প্রলাপে পরিণত হচ্ছে।
অন্যদিকে সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে ছেলেখেলা করার শুরুটা নব্বইয়ের দশকের আগে থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন–বেতারের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। ভিন্নমতের অনেককেই পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সাদা তালিকা থেকে কালো তালিকায় ঢুকতে বা বেরোতে দেখা গেছে। এবং একসময় সেটিই হয়ে গেল জনপ্রিয় ‘সংস্কৃতি’! এভাবেই এ দেশের সংস্কৃতিতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও পক্ষপাতযুক্ত হয়ে গেল। সেটা এতটাই যে, এখন কোনো উদ্যোগে সরকারি অনুদানের খবর পেলেই আমরা তাতে পক্ষ–বিপক্ষের গন্ধ শুঁকি! কারণ সংস্কৃতির দুনিয়ায় এ দেশে বাস্তবানুগ (বাস্তবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু) কোনো কিছু পাওয়া এখন ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে। ফলে এ দেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে (নাটক, সিনেমা, গানসহ) ভাবমূর্তির সংকট দেখা দিয়েছে। এই ভাবমূর্তি ও তার সংকট আবার উভমুখী। কখনও ভাবমূর্তির কারণে সংকটের মুখে পড়েন কেউ কেউ, আবার কখনও কখনও সংকটই ভাবমূর্তিকে বিপদাপন্ন করে ফেলছে।
এই পরিস্থিতি কী একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? উত্তরটি অবশ্যই ‘না’। আমাদের আগের কয়েক প্রজন্মের ব্যর্থতাই আমরা বয়ে চলেছি। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতিতে উপযুক্ত পরিবর্তন না আসার পেছনেও এতদঅঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের অকর্মণ্যতাকেই দায়ী করেছিলেন আহমদ ছফা। তাঁর ভাষায়, ‘তেইশ–চব্বিশ বছর বড় কম সময় নয়। এই সিকি শতাব্দী পরিমাণ সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিটি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যে দু’তিনটি কবিতার বই, দু’তিনটি উপন্যাস, দু’তিনটি প্রবন্ধের সংকলন, দুটি কি তিনটি উল্লেখ করবার মত নাটক বা অ–নাটক এই–ই তো আমাদের মোটামুটি মানস ফসল। এই সাহিত্য নিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হওয়া দূরে থাকুক, সামগ্রিক বাংলা–সাহিত্যের উৎকর্ষের নিরিখে এ আর এমন কি! কালজয়ী এবং দেশজয়ী হওয়ার স্পর্ধা রাখে এমন কোন সাহিত্য এ দেশে রচিত হয়নি।’

তবে হ্যাঁ, সাহিত্যের বিচারে আমরা কিছুটা এগিয়েছি বটে। আমাদের নিজস্ব প্রকাশনা শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তা রুগ্ন বেশ। লেখক তালিকাও দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু তার কতটুকু ‘কালজয়ী’ বা ‘দেশজয়ী’, তা নিয়ে সন্দেহ ভালোমতোই আছে। আবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শহিদুল জহিরদের মতো অনেককে দেশবাসী সময়মতো চিনতেই পারছে না। কারণ অবশ্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসম বিকাশ। সেই বিকাশ সমাজ ও অর্থনীতির পাশাপাশি শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও অসমভাবেই হয়েছে। আমাদের সাহিত্য পুরস্কারগুলো দিনকে দিন স্বজন ও রাজনীতিপ্রীতির চূড়ান্ত প্রদর্শনীর জায়গা হচ্ছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষিত হওয়ার পরই এ নিয়ে গুঞ্জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে, সেলফ সেন্সরশিপে কলম (বা কিবোর্ড) বেঁধে না রেখে কয়জনই বা সাহিত্যচর্চা করেন? ফলে আকালের দিনে আমরা পুষ্পশোভিত সকালের ছবি দেখি, পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাতাবি লেবুর বাম্পার ফলনের গল্প শুনি।
অন্যদিকে এমন ধারার সাহিত্যকর্ম সংখ্যায় বেশি হওয়ায়, ব্যতিক্রমগুলো হারিয়ে যাচ্ছে অতলে। আবার অনুবাদ সাহিত্যে দখলের প্রমাণ শক্তিশালী না হওয়ার দরুণ একদিকে আমরা যেমন বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকছি না, ঠিক তেমনি বাকি বিশ্বও আমাদের সংখ্যার বিচারে কিঞ্চিৎ মানসম্পন্ন সাহিত্য সম্পর্কেও অবগত হচ্ছে না। এ দেশে বেশ কয়েক দশক ধরেই নতুন সাহিত্যকর্মের বিচার হচ্ছে বাজারে বিকিকিনির পরিমাণে, বইমেলা থেকে করা ফেসবুক লাইভের ওয়াচিং লিস্টের সমাগমে। সেসবের মান নিয়ে উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করছে না কেউ বৃত্তচ্যূত হওয়ার ভয়েই। দেশের বিভিন্ন বিষয়ের মতো শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও আমরা পছন্দের বৃত্ত রচনার এক অবিনাশী ‘কালচার’ চালু করেছি। এসব ভাঙা দূরের কথা, বরং এর শনৈ শনৈ বৃদ্ধিতে এই ‘আমাদের’ অবদান দিনকে দিন বাড়ছেই!
বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস নামক রচনায় এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন আহমদ ছফা। তিনি আঙুল তুলেছিলেন কলকাতার পত্র–পত্রিকার দিকে এবং জোর দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে ‘নানা বিষয়ে অনেকগুলো সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশের’ ওপর। ছফার ভাষায়, ‘কিন্তু তা হচ্ছে না, বিনিময়ে কোলকাতার পত্র–পত্রিকা এসে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলছে।’ ছফা একদিকে বলেছেন, তিনি কলকাতার পত্র–পত্রিকা আসার বিরোধী নন। আবার অন্যদিকে বলেছেন, ‘ওদেশের সব পত্র–পত্রিকা ব্যাপক হারে আমাদের দেশে আসতে থাকলে আমাদের দেশে সাময়িকপত্রের জন্ম এবং বিকাশ অনেক কারণে বিঘ্নিত হবে।’ তাঁর মূল আপত্তি ছিল, এ দেশে কলকাতার পত্র–পত্রিকার একাধিপত্য সৃষ্টির বিষয়টিতে। অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলকাতার পত্র–পত্রিকা ‘কাটতি’ভিত্তিক। এক অর্থে এ দেশে পশ্চিমবঙ্গের পত্র–পত্রিকা আসার বিরোধী ছিলেন ছফা। বাহাত্তরের পরও তিনি বইমেলাকে কেন্দ্র করেও এমন বিরোধিতা করেছিলেন বলে সুবিদিত আছে। এ অনেকটা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মতো। এই একই ধরনের প্রতিবাদ আমরা পরবর্তীতে এ দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনেও দেখতে পেয়েছি, যখন বিদেশি চলচ্চিত্র (বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্র) প্রদর্শনের বিরোধিতা করে আন্দোলন হয়। ছফা যেভাবে এ দেশের সাহিত্য অঙ্গনকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণবাদী হতে চেয়েছিলেন, সেভাবে আদৌ কিছু সংরক্ষণ করা যায়? সেই যুক্তিতে তো এক অর্থে বিশ্বসাহিত্য থেকেও দূরে থাকা যায়! কারণ তাতেও যে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়!
এ দেশে অসংখ্য সাময়িকপত্রের যে প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এখানে বিভিন্ন সময় সেই চেষ্টা হয়েছেও বটে। কিন্তু বরাবরই তা থমকে গেছে ওই কাটতির বিচারেই, স্থূলভাবে বললে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই। এবং কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কবি–সাহিত্যিকদের পরস্পরের পিঠ চুলকানো ও একে–অপরের পেছনে লাগার নীতির কারণে। বুদ্ধিজীবী মহলে এই দুই নীতিই একটি সাধারণ বিষয়। অন্যান্য দেশেও এমনটা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মতো সাহিত্যচর্চা মানেই এ দুটিকেই ‘মূল’ ভেবে নেওয়া কবি–সাহিত্যিক সমাজ একাধিক পাওয়া ভার। বর্তমানে এই লক্ষণ আরও প্রকট হয়েছে।
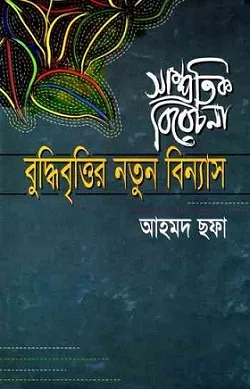
আহমদ ছফার এই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের এ দেশে সঞ্চালনের ঘোরতর বিরোধিতা কি দেশভাগের আগের তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্সের ফলাফল? হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাবু কালচারের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের অন্যতম প্রধান শিকার পূর্ববঙ্গ হয়েছিল, সাহিত্য–রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রেই। হয়তো সেটিই ছফার মনে গেড়ে বসেছিল। নইলে তিনি হয়তো মান দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে চাইতেন, খালি মাঠে গোল দিতে নয়। আর যাই হোক, দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রম বা বিভ্রম বা সত্য—কোনোটাই রোখার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।
সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের এই প্ররোচনা হয়তো আহমদ ছফা তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম অক্ষশক্তি সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া থেকেই পেয়েছিলেন। পাওয়াটা স্বাভাবিকও। তবে এ দেশের সমাজ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সেটি কতটুকু যুক্তিসংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অর্ন্তভুক্ত অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বের পণ্য ও নীতির প্রতি এক ধরনের অন্ধ বিরোধিতা এবং নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। সেই সংরক্ষণবাদী ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার কিঞ্চিৎ উপকার বাদে অপকারিতাই হয়েছে বেশি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। এই মানবচরিত্রকে অস্বীকার করে কোনো ‘মহৎ’ উদ্দেশ্যই সফল হওয়ার নয়।
তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মতো তুর্কি দেশে কামাল আতাতুর্কের আনা সমাজ বিপ্লবের প্রতিও অকুণ্ঠ প্রশংসা ধরা পড়ে আহমদ ছফার লেখায়। এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার বারংবার উল্লেখপূর্বক এ দেশে তেমনি নতুন ঘরানার বিপ্লব আনার প্রয়োজনীয়তার কথা ছফা তাঁর ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’–এ তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই দুই ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আসলে কতটুকু? এ দেশের জন্ম কোনো জার বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হয়নি, বরং একটি শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হয়েছে। ফলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্যা হলো, এ দেশে যে কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টা বা পরিবর্তন প্রক্রিয়াই অন্যের ‘কপি ক্যাট’ দোষে দুষ্ট। ফলে কখনোই নিজস্ব কোনো দর্শন আমরা তৈরি করতে পারিনি। এবং এই অক্ষমতার কারণেই আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাস অনেকাংশেই অনুকরণের ইতিহাস। তাতে নিজস্ব ভাবনা–চিন্তাও বেশ কম তাই অনুমিতভাবেই। এই একই কথা অবশ্য ছফাও স্বীকীর করেছেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করছি। আমাদের সবদিকে উদ্ভাবনীশক্তির উদ্বোধনের বদলে আমরা অপরের অনুকরণ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। ভালো জিনিস অনুকরণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কিন্তু অন্ধ অনুকরণটা কি কখনো ভালো?’
এক কথায় তবে বর্তমানে এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাসটি কেমন? নিজেকে জড়িয়েই উদাহরণ দিই। ১৯৭২ সালে লেখা ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’–এ ছফা সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশে কী ধরনের ধর্মীয় সংস্কার প্রয়োজন, তা নিয়েও বিস্তর কথা বলেছিলেন। তাঁর অন্যতম মন্তব্য ছিল, ‘বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তার কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। এখন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে বাংলাদেশের ধর্মের বদ্ধমতগুলো উড়িয়ে দিতে পারলে মানুষে মানুষে অন্তরের মিলনটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।’ ছফা মনে করেছিলেন, মানুষ শুধু মানুষ—এই পরিচয়ে চিহ্নিত করার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস ও প্রক্রিয়াটি দেশে শুরু হয়েছিল।
কিন্তু ঠিক ৫০ বছর পরে এসে এই আমি ছফার বাহাত্তরে লেখা ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় ঢুকতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনিরাপদ বোধ করতে বাধ্য হই। এই ৫০ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাকে প্রবলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ‘ওসব নিয়ে কথা বলো না, বিপদ আছে!’ আমাকে হামলা দেখানো হয়েছে, রক্ত দেখানো হয়েছে, বইমেলায় ঘুরতে গিয়ে লাশ হয়ে যাওয়া দেখানো হয়েছে। এবং মনের গহীনে এই গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে—‘চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!’
এবার আপনারাই না–হয় ঠিক করুন, মানুষ শুধু মানুষ—এই প্রক্রিয়ায় আমরা এগিয়েছি নাকি ব্যাপক পিছিয়ে ফিরে গেছি অসহনশীল সেই নিষ্ঠুর পুরনো অযৌক্তিক বাস্তবতায়?
এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাসের প্রকৃত রূপ।
লেখক: বার্তা সম্পাদক, চরচা


‘বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ–কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।’
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাস নিয়ে লিখতে বসে শুরুতেই এমন মন্তব্য করেছিলেন কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং সর্বতোভাবে একজন স্বাধীন চিন্তক আহমদ ছফা। ১৯৭২ সালে তিনি লিখেছিলেন ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হওয়ার পর এ নিয়ে বইও বের হয়েছিল। এই রচনাটির ৫০ বছর পূর্তিও হয়ে গেছে। চলুন, এখন একটু পেছন ফিরে এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির আদি ধারা অবলোকন করা যাক এবং অবশ্যই তার পাশাপাশি বর্তমান ধারার একটি তুলনামূলক আলোচনাও থাকবে।
প্রশ্ন উঠতে পারে, আহমদ ছফার ৫০ বছর আগের দেওয়া বক্তব্য আমরা কি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করে নেব? যেমন আপত্তি জানানো যেতেই পারে, তেমনি ছফার বেশ কিছু বিশ্লেষণ যুক্তির বিচারে গ্রহণ করে নেওয়াই শ্রেয়। ছফা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিবৃত্তির তৎকালীন বিন্যাসকে আতশ কাঁচের নিচে নিয়েছিলেন। তাতে ক্ষুরধার সমালোচনা ছিল। হ্যাঁ পাঠক, সত্যিই সেই সমালোচনায় ধার ছিল, মরচে নয়। এবং তাতে অনেকের আঁতে ঘা লেগেছিল এবং এখনও নিশ্চিতভাবেই লাগে।
১৯৭২ সালে লেখা ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’ রচনায় আহমদ ছফা তৎকালীন বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীদের ‘পাকিস্তানি’ মানসিকতার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদ। ছফার কথায়, বাংলাদেশের উন্মেষকালে এখানকার বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর হামলা বা বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টার প্রশ্নে কিছু ‘পোশাকি’ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করার কারণে বুদ্ধিজীবীদের কাউকে চাকরি হারাতে হয়েছে বা জেলে যেতে হয়েছে—এমন কোনো মানুষের নাম জানার সৌভাগ্য হয়নি বলে দাবি করেছিলেন ছফা। তাঁর আরও অনুযোগ ছিল যে, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজের ‘অনেক গভীর, বিকট হাঁ করা’ প্রশ্নের বিষয়ে এক–দুজন ব্যতীত কোনো ‘প্রতিষ্ঠাবান’ বুদ্ধিজীবীই উচ্চবাচ্য করেননি। এসবের কারণ হিসেবে ছফা যেমন সাংস্কৃতিক এলিট শ্রেণির সুবিধাবাদী মনোভাবকে দায়ী করেছেন, তেমনি তৎকালীন শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের অপরিণত ভূমিকা এবং স্নায়ুযুদ্ধের কবলে পড়া বিশ্বের বিভিন্ন অক্ষশক্তির (যেমন: মার্কিন ডলার) হয়ে কাজ করাকেও দায়ী করেছেন। এসেছে ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও দূরদর্শিতার অভাবের দরুণ ধীরে ধীরে সংস্কৃতি এবং রাজনীতি একে–অপরের পরিপূরক না হয়ে দুটি আলাদা জলঅচল কুঠুরিতে পরিণত’ হওয়ার বিষয়টিও।

মজার বিষয় হলো, ৫০ বছর পরও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সমস্যা সেই সুবিধাবাদই। এ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর সজোরে আওয়াজ তোলেননি। যে ব্যক্তিকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে পুরো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন হলো, তাতেও খুব জোরালোভাবে একযোগে প্রতিবাদ আসেনি এ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে। হয়তো তখনকার ভয়ের আবহকে কারণ হিসেবে দেখাতে চাইবেন অনেকে, কিন্তু যেকোনো ভয়ের জাল ছিঁড়ে আত্মপ্রকাশ করাই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল কাজ। তবে হ্যাঁ, এ দেশে আনুষ্ঠানিক সামরিক শাসনামলের শেষের দিকে আমরা তার কিছুটা দেখতে পেয়েছি। সে সময় কেউ কেউ যেমন বিক্রিও হয়েছেন, অনেকেই আবার গণতন্ত্রে ফিরতে প্রতিবাদে মুখরও হয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে ফেরার পরই সেই একমুখী প্রতিবাদ, বহুমুখী সুবিধাবাদে ফের আটকে যায়। ১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের (কবি–সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী প্রমুখ) নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখেছি এবং এখনও দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব বুদ্ধিজীবীর একদম নিজের ঘরের চালে আগুন না লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা মুখ খোলেন না। এ দেশে এখন কবি–সাহিত্যিকদের চেয়েচিন্তে পুরস্কার নিতে দেখা যায়। সাংবাদিকেরা নিরপেক্ষতার ভিত্তিমূল ভেঙেচুরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের বয়ানে নিজেদের পেশাভিত্তিক সংগঠনকে দু ভাগ করে এক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বা ভেতরে আলাদা আলাদা সমাবেশ করেন। কেউ বলেন, দেশ ভালো চলছে। কেউ আবার সমালোচনা করতে গিয়ে ভালো–মন্দের বিচারক্ষমতা আর বজায় রাখেন না। এই দুই পক্ষ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মতো নিজেদের রাজনৈতিক পথের সুপ্রশংসা করে যান, তাতে যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক! আর যারা এসবে নেই, তারা কেউ কেউ করপোরেট গোলামি করছেন। কিন্তু কয়জন আর শুধু সাংবাদিকতার মূলনীতির নিরিখে সাংবাদিকতা করছেন? সংখ্যাটা বোধহয় আঙুলের কর গুণেই বের করা সম্ভব হবে। আর এসবের মূল কারণ সর্বতোভাবে সে–ই কলাটা–মুলোটা।
একই অবস্থা দেখা যাবে শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী প্রমুখদের মধ্যে। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ নীল। দলবাজি এতটাই করুণ অবস্থায় গেছে যে, ভিন্নমতের কারও ছায়াও মাড়াতে চান না কেউ, যুক্তি দিয়ে সমালোচনা তো দূরের কথা। তাদের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষভাবে শিক্ষাদানটাও করতে পারেন কিনা সন্দেহ। কীভাবে পারবেন? কেউ কেউ যে রাজনৈতিক দলের কৌশল নির্ধারণের কান্ডারির ভূমিকাও নিচ্ছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। প্রায় ৮/১০ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকু বলতে পারি যে, আজকালকার শিক্ষকদের মধ্যে কিয়দংশই মেরুদণ্ড সোজা রেখে হক কথাটা কইতে পারেন না। কেউ কেউ শ্রেণিকক্ষে ‘সেকুলারিজম’–এর সঠিক অর্থটি বলতেও ভয় পান! দু–একজন যে একদম নেই, তা নয়। কিন্তু তাদের গলায় আমরাই পরাচ্ছি জুতার মালা। ফলে হাজার হাজারের সত্যের অপলাপের বিপরীতে দু–একজনের সত্যকথন একসময় প্রলাপে পরিণত হচ্ছে।
অন্যদিকে সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে ছেলেখেলা করার শুরুটা নব্বইয়ের দশকের আগে থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন–বেতারের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। ভিন্নমতের অনেককেই পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সাদা তালিকা থেকে কালো তালিকায় ঢুকতে বা বেরোতে দেখা গেছে। এবং একসময় সেটিই হয়ে গেল জনপ্রিয় ‘সংস্কৃতি’! এভাবেই এ দেশের সংস্কৃতিতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও পক্ষপাতযুক্ত হয়ে গেল। সেটা এতটাই যে, এখন কোনো উদ্যোগে সরকারি অনুদানের খবর পেলেই আমরা তাতে পক্ষ–বিপক্ষের গন্ধ শুঁকি! কারণ সংস্কৃতির দুনিয়ায় এ দেশে বাস্তবানুগ (বাস্তবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু) কোনো কিছু পাওয়া এখন ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে। ফলে এ দেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে (নাটক, সিনেমা, গানসহ) ভাবমূর্তির সংকট দেখা দিয়েছে। এই ভাবমূর্তি ও তার সংকট আবার উভমুখী। কখনও ভাবমূর্তির কারণে সংকটের মুখে পড়েন কেউ কেউ, আবার কখনও কখনও সংকটই ভাবমূর্তিকে বিপদাপন্ন করে ফেলছে।
এই পরিস্থিতি কী একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? উত্তরটি অবশ্যই ‘না’। আমাদের আগের কয়েক প্রজন্মের ব্যর্থতাই আমরা বয়ে চলেছি। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতিতে উপযুক্ত পরিবর্তন না আসার পেছনেও এতদঅঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের অকর্মণ্যতাকেই দায়ী করেছিলেন আহমদ ছফা। তাঁর ভাষায়, ‘তেইশ–চব্বিশ বছর বড় কম সময় নয়। এই সিকি শতাব্দী পরিমাণ সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিটি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যে দু’তিনটি কবিতার বই, দু’তিনটি উপন্যাস, দু’তিনটি প্রবন্ধের সংকলন, দুটি কি তিনটি উল্লেখ করবার মত নাটক বা অ–নাটক এই–ই তো আমাদের মোটামুটি মানস ফসল। এই সাহিত্য নিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হওয়া দূরে থাকুক, সামগ্রিক বাংলা–সাহিত্যের উৎকর্ষের নিরিখে এ আর এমন কি! কালজয়ী এবং দেশজয়ী হওয়ার স্পর্ধা রাখে এমন কোন সাহিত্য এ দেশে রচিত হয়নি।’

তবে হ্যাঁ, সাহিত্যের বিচারে আমরা কিছুটা এগিয়েছি বটে। আমাদের নিজস্ব প্রকাশনা শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তা রুগ্ন বেশ। লেখক তালিকাও দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু তার কতটুকু ‘কালজয়ী’ বা ‘দেশজয়ী’, তা নিয়ে সন্দেহ ভালোমতোই আছে। আবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শহিদুল জহিরদের মতো অনেককে দেশবাসী সময়মতো চিনতেই পারছে না। কারণ অবশ্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসম বিকাশ। সেই বিকাশ সমাজ ও অর্থনীতির পাশাপাশি শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও অসমভাবেই হয়েছে। আমাদের সাহিত্য পুরস্কারগুলো দিনকে দিন স্বজন ও রাজনীতিপ্রীতির চূড়ান্ত প্রদর্শনীর জায়গা হচ্ছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষিত হওয়ার পরই এ নিয়ে গুঞ্জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে, সেলফ সেন্সরশিপে কলম (বা কিবোর্ড) বেঁধে না রেখে কয়জনই বা সাহিত্যচর্চা করেন? ফলে আকালের দিনে আমরা পুষ্পশোভিত সকালের ছবি দেখি, পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাতাবি লেবুর বাম্পার ফলনের গল্প শুনি।
অন্যদিকে এমন ধারার সাহিত্যকর্ম সংখ্যায় বেশি হওয়ায়, ব্যতিক্রমগুলো হারিয়ে যাচ্ছে অতলে। আবার অনুবাদ সাহিত্যে দখলের প্রমাণ শক্তিশালী না হওয়ার দরুণ একদিকে আমরা যেমন বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকছি না, ঠিক তেমনি বাকি বিশ্বও আমাদের সংখ্যার বিচারে কিঞ্চিৎ মানসম্পন্ন সাহিত্য সম্পর্কেও অবগত হচ্ছে না। এ দেশে বেশ কয়েক দশক ধরেই নতুন সাহিত্যকর্মের বিচার হচ্ছে বাজারে বিকিকিনির পরিমাণে, বইমেলা থেকে করা ফেসবুক লাইভের ওয়াচিং লিস্টের সমাগমে। সেসবের মান নিয়ে উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করছে না কেউ বৃত্তচ্যূত হওয়ার ভয়েই। দেশের বিভিন্ন বিষয়ের মতো শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও আমরা পছন্দের বৃত্ত রচনার এক অবিনাশী ‘কালচার’ চালু করেছি। এসব ভাঙা দূরের কথা, বরং এর শনৈ শনৈ বৃদ্ধিতে এই ‘আমাদের’ অবদান দিনকে দিন বাড়ছেই!
বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস নামক রচনায় এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন আহমদ ছফা। তিনি আঙুল তুলেছিলেন কলকাতার পত্র–পত্রিকার দিকে এবং জোর দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে ‘নানা বিষয়ে অনেকগুলো সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশের’ ওপর। ছফার ভাষায়, ‘কিন্তু তা হচ্ছে না, বিনিময়ে কোলকাতার পত্র–পত্রিকা এসে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলছে।’ ছফা একদিকে বলেছেন, তিনি কলকাতার পত্র–পত্রিকা আসার বিরোধী নন। আবার অন্যদিকে বলেছেন, ‘ওদেশের সব পত্র–পত্রিকা ব্যাপক হারে আমাদের দেশে আসতে থাকলে আমাদের দেশে সাময়িকপত্রের জন্ম এবং বিকাশ অনেক কারণে বিঘ্নিত হবে।’ তাঁর মূল আপত্তি ছিল, এ দেশে কলকাতার পত্র–পত্রিকার একাধিপত্য সৃষ্টির বিষয়টিতে। অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলকাতার পত্র–পত্রিকা ‘কাটতি’ভিত্তিক। এক অর্থে এ দেশে পশ্চিমবঙ্গের পত্র–পত্রিকা আসার বিরোধী ছিলেন ছফা। বাহাত্তরের পরও তিনি বইমেলাকে কেন্দ্র করেও এমন বিরোধিতা করেছিলেন বলে সুবিদিত আছে। এ অনেকটা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মতো। এই একই ধরনের প্রতিবাদ আমরা পরবর্তীতে এ দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনেও দেখতে পেয়েছি, যখন বিদেশি চলচ্চিত্র (বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্র) প্রদর্শনের বিরোধিতা করে আন্দোলন হয়। ছফা যেভাবে এ দেশের সাহিত্য অঙ্গনকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণবাদী হতে চেয়েছিলেন, সেভাবে আদৌ কিছু সংরক্ষণ করা যায়? সেই যুক্তিতে তো এক অর্থে বিশ্বসাহিত্য থেকেও দূরে থাকা যায়! কারণ তাতেও যে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়!
এ দেশে অসংখ্য সাময়িকপত্রের যে প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এখানে বিভিন্ন সময় সেই চেষ্টা হয়েছেও বটে। কিন্তু বরাবরই তা থমকে গেছে ওই কাটতির বিচারেই, স্থূলভাবে বললে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই। এবং কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কবি–সাহিত্যিকদের পরস্পরের পিঠ চুলকানো ও একে–অপরের পেছনে লাগার নীতির কারণে। বুদ্ধিজীবী মহলে এই দুই নীতিই একটি সাধারণ বিষয়। অন্যান্য দেশেও এমনটা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মতো সাহিত্যচর্চা মানেই এ দুটিকেই ‘মূল’ ভেবে নেওয়া কবি–সাহিত্যিক সমাজ একাধিক পাওয়া ভার। বর্তমানে এই লক্ষণ আরও প্রকট হয়েছে।
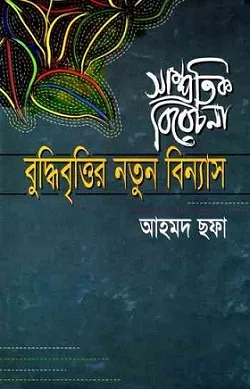
আহমদ ছফার এই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের এ দেশে সঞ্চালনের ঘোরতর বিরোধিতা কি দেশভাগের আগের তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্সের ফলাফল? হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাবু কালচারের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের অন্যতম প্রধান শিকার পূর্ববঙ্গ হয়েছিল, সাহিত্য–রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রেই। হয়তো সেটিই ছফার মনে গেড়ে বসেছিল। নইলে তিনি হয়তো মান দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে চাইতেন, খালি মাঠে গোল দিতে নয়। আর যাই হোক, দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রম বা বিভ্রম বা সত্য—কোনোটাই রোখার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।
সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের এই প্ররোচনা হয়তো আহমদ ছফা তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম অক্ষশক্তি সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া থেকেই পেয়েছিলেন। পাওয়াটা স্বাভাবিকও। তবে এ দেশের সমাজ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সেটি কতটুকু যুক্তিসংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অর্ন্তভুক্ত অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বের পণ্য ও নীতির প্রতি এক ধরনের অন্ধ বিরোধিতা এবং নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। সেই সংরক্ষণবাদী ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার কিঞ্চিৎ উপকার বাদে অপকারিতাই হয়েছে বেশি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। এই মানবচরিত্রকে অস্বীকার করে কোনো ‘মহৎ’ উদ্দেশ্যই সফল হওয়ার নয়।
তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মতো তুর্কি দেশে কামাল আতাতুর্কের আনা সমাজ বিপ্লবের প্রতিও অকুণ্ঠ প্রশংসা ধরা পড়ে আহমদ ছফার লেখায়। এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার বারংবার উল্লেখপূর্বক এ দেশে তেমনি নতুন ঘরানার বিপ্লব আনার প্রয়োজনীয়তার কথা ছফা তাঁর ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’–এ তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই দুই ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আসলে কতটুকু? এ দেশের জন্ম কোনো জার বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হয়নি, বরং একটি শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হয়েছে। ফলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্যা হলো, এ দেশে যে কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টা বা পরিবর্তন প্রক্রিয়াই অন্যের ‘কপি ক্যাট’ দোষে দুষ্ট। ফলে কখনোই নিজস্ব কোনো দর্শন আমরা তৈরি করতে পারিনি। এবং এই অক্ষমতার কারণেই আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাস অনেকাংশেই অনুকরণের ইতিহাস। তাতে নিজস্ব ভাবনা–চিন্তাও বেশ কম তাই অনুমিতভাবেই। এই একই কথা অবশ্য ছফাও স্বীকীর করেছেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করছি। আমাদের সবদিকে উদ্ভাবনীশক্তির উদ্বোধনের বদলে আমরা অপরের অনুকরণ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। ভালো জিনিস অনুকরণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কিন্তু অন্ধ অনুকরণটা কি কখনো ভালো?’
এক কথায় তবে বর্তমানে এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাসটি কেমন? নিজেকে জড়িয়েই উদাহরণ দিই। ১৯৭২ সালে লেখা ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’–এ ছফা সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশে কী ধরনের ধর্মীয় সংস্কার প্রয়োজন, তা নিয়েও বিস্তর কথা বলেছিলেন। তাঁর অন্যতম মন্তব্য ছিল, ‘বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তার কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। এখন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে বাংলাদেশের ধর্মের বদ্ধমতগুলো উড়িয়ে দিতে পারলে মানুষে মানুষে অন্তরের মিলনটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।’ ছফা মনে করেছিলেন, মানুষ শুধু মানুষ—এই পরিচয়ে চিহ্নিত করার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস ও প্রক্রিয়াটি দেশে শুরু হয়েছিল।
কিন্তু ঠিক ৫০ বছর পরে এসে এই আমি ছফার বাহাত্তরে লেখা ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কার বিষয়ক আলোচনায় ঢুকতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনিরাপদ বোধ করতে বাধ্য হই। এই ৫০ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাকে প্রবলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ‘ওসব নিয়ে কথা বলো না, বিপদ আছে!’ আমাকে হামলা দেখানো হয়েছে, রক্ত দেখানো হয়েছে, বইমেলায় ঘুরতে গিয়ে লাশ হয়ে যাওয়া দেখানো হয়েছে। এবং মনের গহীনে এই গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে—‘চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!’
এবার আপনারাই না–হয় ঠিক করুন, মানুষ শুধু মানুষ—এই প্রক্রিয়ায় আমরা এগিয়েছি নাকি ব্যাপক পিছিয়ে ফিরে গেছি অসহনশীল সেই নিষ্ঠুর পুরনো অযৌক্তিক বাস্তবতায়?
এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাসের প্রকৃত রূপ।
লেখক: বার্তা সম্পাদক, চরচা
সম্পর্কিত

চীন কি ইরানকে বাঁচাতে আসবে?
ইরান এবং মার্কিন-ইসরায়েল জোটের মধ্যকার উত্তেজনা এখন এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী, সংবাদকক্ষ এবং নীতি-নির্ধারণী মহলে একটি প্রশ্ন নিয়েই বেশ গুঞ্জন চলছে: চীন কি শেষ পর্যন্ত ইরানের রক্ষাকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসবে? আর যদি আসে, তবে সেই সহায়তার ধরণ কেমন হবে?

ইরানে ট্রাম্পের হামলা যে ভয়ের জন্ম দিচ্ছে
ইরানি বাহিনীর হাতের কাছেই বহু লক্ষ্যবস্তু আছে। এর মধ্যে রয়েছে–হরমুজ প্রণালী বা বৃহত্তর উপসাগরে সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজ। নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা তেহরানের মিত্র ইয়েমেনের হুতি বাহিনীর ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল, যাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট

