ডনরো ডকট্রিনের কোনো ‘মানে নেই’

ডনরো ডকট্রিনের কোনো ‘মানে নেই’
স্টিফেন এম. ওয়াল্ট

ভেনেজুয়েলার প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান নীতির কৌশলগত যৌক্তিকতা নিয়ে আপনি যদি বিভ্রান্ত বোধ করেন, তবে আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সাম্প্রতিক ‘অপহরণের’বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই হাস্যকর।
এই অভিযানের পেছনে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদ’ থেকে আমেরিকাকে রক্ষা করার যে দাবি করা হচ্ছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। ভেনেজুয়েলা কখনোই যুক্তরাষ্ট্রে আসা অবৈধ মাদকের (বিশেষ করে ফেন্টানিলের) উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল না। মাদকের বিস্তার রোধে ট্রাম্প আসলে কতটুকু আন্তরিক, তা বোঝা যায় সাবেক হন্ডুরান প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকে তার দেওয়া ‘প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমা’ থেকে, যিনি কি না মার্কিন আদালতেই মাদক পাচারের দায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন।
মার্কিন বিচার বিভাগ এখন নিজেরাই স্বীকার করছে যে, তথাকথিত বিপজ্জনক মাদক কার্টেল ‘কার্টেল দে লস সোলেস’-এর বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। অথচ গত এক বছর ধরে ট্রাম্প প্রশাসন এই কাল্পনিক কার্টেলের নাম জপছিল। সহজ কথায়, এটি ছিল প্রশাসনের সাজানো একটি বানোয়াট প্রোপাগান্ডা। এটি ইরাকে সেই ‘গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র’ খোঁজার গল্পের মতোই অলীক। এর ভয় দেখিয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করা হলেও শেষ পর্যন্ত যার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি।
মাদুরোকে বন্দী করার পেছনে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তাকে সুসংহত করার কোনো বাস্তবসম্মত যুক্তিও নেই। ভেনেজুয়েলা কতটা দুর্বল একটি দেশ, তা মাদুরোকে অতি সহজে আটকের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। দেশটি আমেরিকার শক্তিশালী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘনিষ্ঠ কৌশলগত মিত্রও নয়। সেখানে চীন কোনো সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করছিল না বা ইরানও আমেরিকায় আঘাত হানার জন্য কোনো ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেনি। এমনকি মার্কিন বাণিজ্য পথকে বাধাগ্রস্ত করার মতো কোনো শক্তিশালী নৌবাহিনীও তাদের নেই। সত্যি বলতে, কারাকাস থেকে আসা কোনো ‘ভয়াবহ হুমকির’কথা ভেবে কেউ কখনো রাতে নির্ঘুম কাটায়নি, আর মাদুরো এখন ব্রুকলিনের কারাগারে বন্দি বলে আমাদের নিরাপত্তা রাতারাতি বেড়ে গেছে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই।
এমনকি এই অভিযানের পেছনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কোনো মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল না। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোকে ক্ষমতায় বসানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। বরং তিনি মাদুরোরই এক সহকারীর সাথে আপস করতে আগ্রহী, যার নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা এখনো অনস্বীকার্যভাবে একটি স্বৈরাচারী কাঠামো। সুতরাং, গণতন্ত্রের দোহাই দেওয়াটা এখানে কেবল একটি অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়।
বিপজ্জনক মাদক নির্মূল, নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলা বা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার,যদি এর কোনোটিই মূল উদ্দেশ্য না হয়; তবে কি তেলের কারণেই এই অভিযান? ট্রাম্পের দাবি অন্তত তেমনই। তিনি বারবার বলছেন এটাই আসল কারণ এবং মার্কিন কোম্পানিগুলো সেখানে ঢুকে তেলের দখল নিয়ে আমেরিকাকে আরও মহান করবে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। ট্রাম্প নিজের খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে 'আঙ্কেল স্যাম'-এর পকেটে ভেনেজুয়েলার তেল থেকে বড় কোনো মুনাফা আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সম্প্রতি তিনি বড়াই করে বলেছিলেন, ভেনেজুয়েলা আমেরিকাকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল দিতে রাজি হয়েছে। শুনতে এটি বিশাল মনে হলেও বাস্তবে তা আমেরিকায় মাত্র চার দিনের তেল উৎপাদনের সমান। ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন যে, তিনি এই তেল বিক্রির অর্থ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তা ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি পুনর্গঠনে ব্যয় করবেন। কেউ যদি এটি বিশ্বাস করেন, তবে বুঝতে হবে ট্রাম্পের শিকারি মানসিকতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আর যদি সত্যিই সেই অর্থ পাওয়া যায়, তবুও ভেনেজুয়েলার বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের বিশাল খরচের তুলনায় তা হবে ‘সমুদ্রের এক ফোঁটা পানির’ মতো নগণ্য।

এটা ঠিক যে ভেনেজুয়েলায় বিশ্বের বৃহত্তম তেলের মজুদ রয়েছে। কিন্তু সেখানকার তেল মূলত ‘ভারী অপরিশোধিত’। এটি মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা যেমন কঠিন, পরিশোধন করাও তেমনি ব্যয়বহুল। সত্যি বলতে, ভেনেজুয়েলার জরাজীর্ণ অবকাঠামো এবং বিশ্ববাজারে তেলের বর্তমান নিম্নমূল্য বিবেচনায় কোনো বুদ্ধিমান উৎপাদনকারী এই তেল স্পর্শ করার কথা ভাববে না। আর যদি কোনো অলৌকিক ঘটনায় প্রচুর পরিমাণ ভেনেজুয়েলান তেল বিশ্ববাজারে চলে আসে, তবে তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবে। এতে আমেরিকারই ক্ষতি হবে। কারণ দাম কমে যাওয়ায় আমেরিকার অনেক প্রান্তিক ‘শেল অয়েল’ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।
আর ভুলে গেলে চলবে না যে, ট্রাম্প এবং বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো যা-ই ভাবুক না কেন, বর্তমান বিশ্ব ধীর ধীরে হাইড্রোকার্বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শক্তির অন্যান্য উৎসের দিকে ঝুঁকছে। এই পরিবর্তন ভেনেজুয়েলার তেলের মজুদের দামকে দিন দিন আরও কমিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, জলবায়ু পরিবর্তনের কঠোর বাস্তবতায় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ওই তেলের সিংহভাগ মাটির নিচেই রেখে দেওয়া। চীন যখন ভবিষ্যতের পরিবেশবান্ধব শিল্পে আধিপত্য বিস্তারে লেজারের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে এবং বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বাড়াচ্ছে, তখন ট্রাম্প ও তার চারপাশের তথাকথিত ‘কৌশলগত প্রতিভাবানেরা’ গ্রহের জন্য হুমকিস্বরূপ গত শতাব্দীর সেই সেকেলে জ্বালানি নীতি আঁকড়ে ধরছেন।
তাই এই অভিযানের কৌশলগত যৌক্তিকতা নিয়ে আপনার মনে বিভ্রান্তি জাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ এখানে একমাত্র যে কৌশলগত উদ্দেশ্যটি দৃশ্যমান, তা হলো পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি চেষ্টা। যেহেতু ট্রাম্প সবকিছুর ওপর নিজের নামের সিল বসিয়ে নিজের এলাকা বা প্রভাব জাহির করতে পছন্দ করেন, তাই এই ধারণাটিকে এখন ‘ডনরো ডকট্রিন’ হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে। এমনকি সাম্প্রতিক ‘জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল’-এও এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি হয়তো শুনতে এমন এক যুক্তিসঙ্গত ধারণা মনে হতে পারে যা পররাষ্ট্রনীতির বাস্তববাদীরা সমর্থন করবেন, কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে এটিও টিকবে না।

ঐতিহাসিক 'মনরো ডকট্রিন'-এর মূল লক্ষ্য ছিল এটি নিশ্চিত করা যেন পশ্চিম গোলার্ধে অন্য কোনো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তা করতে না হয়। প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এই গোলার্ধ থেকে অন্য সব মহাশক্তিকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং ইতিহাসবিদ সি. ভ্যান উডওয়ার্ডের ভাষায় ‘ফ্রি সিকিউরিটি’র এক অনন্য সুযোগ ভোগ করতে শুরু করে।
তবে ট্রাম্প অ্যান্ড কোম্পানির বর্তমান আলাপচারিতা সেই পুরোনো উদ্দেশ্যকে ধারণ করে না; কারণ বর্তমানে পশ্চিম গোলার্ধে অন্য কোনো মহাশক্তির তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সামরিক উপস্থিতি নেই, আর কেউ তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছে না। বরং ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি’ থেকে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ট্রাম্প প্রশাসন তার প্রতিবেশী দেশগুলোকে আজ্ঞাবহ করতে চায়, যাতে যেকোনো ইস্যুতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলে। মাদুরোর উত্তরসূরিদের তারা এখন সরাসরি এই বার্তাই দিচ্ছে- “আমাদের শর্ত মেনে নাও, নতুবা আমরা অবরোধ জারি রাখব এবং পরিস্থিতি হয়তো আরও ভয়াবহ করে তুলব।” ওয়াশিংটন আশা করছে, তারা আশা করছে যে, ওই অঞ্চলের বাকি দেশগুলোও এই বার্তা পাবে এবং বাধ্য হয়ে অনুগত থাকবে।
বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি এমন সব উদ্যোগে ‘ভেটো’ দেওয়ার অধিকার দাবি করছে, যা ওই রাষ্ট্রগুলোর জন্য কিংবা চীনের মতো দেশের জন্য লাভজনক হতে পারে। ‘জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল’ -এর ভাষ্যমতে, “আমরা এমন একটি গোলার্ধ চাই যা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি অনুপ্রবেশ বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের বিদেশি মালিকানা থেকে মুক্ত থাকবে।” তারা আরও স্পষ্ট করেছে যে, বাইরের কোনো শক্তিকে ‘কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ’ দেওয়া যাবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে গোলার্ধের বাইরের প্রতিযোগীরা এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। ট্রাম্প প্রশাসন বুঝতে পারছে যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো মূলত কম খরচ এবং সহজ শর্তের কারণে চীনের সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু উদার প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ট্রাম্প প্রশাসন হুমকি ও চাপের মুখে ওই দেশগুলোকে এই সহায়তা “প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য” করার নীতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু এই প্রশাসন মূলত একটি স্বার্থলোভী ও অনুদান-বিরোধী মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত, তাই তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের পকেট ভারী করতে চায়; আর এই উদ্দেশ্য হাসিলে তারা উদারতার পরিবর্তে কেবল ভীতির ওপর নির্ভর করছে।
সমস্যা হলো, আমেরিকা যদি প্রতিবেশীদের অর্থনীতিতে এভাবে খবরদারি শুরু করে, তবে সেখানকার যেকোনো বিপর্যয়ের দায় শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের কাঁধেই এসে পড়বে। তারা যদি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে সস্তা ও উন্নত মানের চীনা পণ্য (যেমন: বৈদ্যুতিক গাড়ি) কেনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে, তবে সেখানকার সাধারণ ভোক্তারা চরম অসন্তুষ্ট হবে। একইভাবে, যদি স্থানীয় সরকারগুলোকে চীনা বা বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করা হয় যা কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরি ছিল। তবে সেই অভাব ওয়াশিংটনকেই পূরণ করতে হবে। তা না পারলে লাতিন আমেরিকানদের দারিদ্র্যের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করা হবে। এর সাথে যখন অভিবাসীদের ওপর দোষ চাপানো এবং তাদের গণহারে বিতাড়িত করার প্রশাসনিক জেদ যুক্ত হয়, তখন তা কোনো স্থিতিশীল আধিপত্য তৈরি করে না। বরং এটি হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান মার্কিন-বিদ্বেষ এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার এক চরম প্রেসক্রিপশন।
আমেরিকার অতীতের সফল পররাষ্ট্রনীতিগুলোর সাথে বর্তমান পরিস্থিতির বৈসাদৃশ্য আকাশ-পাতাল। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ইউরোপ ও এশিয়ায় (এমনকি সাবেক শত্রু জার্মানি ও জাপানের সাথেও) অত্যন্ত ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছিল। এর আংশিক কারণ ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আসা একটি অভিন্ন নিরাপত্তা হুমকি। আমেরিকা অত্যন্ত উদারভাবে কাজ করেছিল যাতে তার নতুন অংশীদাররা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে দ্রুত সময়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ট্রাম্পের অভিধানে ‘উদারতা’বা ‘পরোপকার’ বলতে কোনো শব্দ নেই; জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত- “আমার যা আছে তা আমারই, আর তোমার যা আছে তা আলোচনা সাপেক্ষ (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেওয়ার যোগ্য)।”
বন্দুকের মুখে পশ্চিম গোলার্ধ শাসন করার এই নীতি অতীতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার চেয়ে ভালো কোনো ফল বয়ে আনবে না। ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার মনে করেন ইতিহাসের অন্যতম এক ‘অমোঘ বিধান’ বা আয়রন ল হলো, পৃথিবী কেবল ‘শক্তি’ বা ক্ষমতার দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু তিনি ইতিহাসের সেই অমোঘ সত্যটি ভুলে গেছেন যা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আর তা হলো- যেসব নেতা মনে করেন ক্ষমতাই শেষ কথা, তারা অবধারিতভাবে একের পর এক বোকামি করে বসেন।
লেখক: ‘ফরেন পলিসি’ ম্যাগাজিনের কলামিস্ট এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক


ভেনেজুয়েলার প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান নীতির কৌশলগত যৌক্তিকতা নিয়ে আপনি যদি বিভ্রান্ত বোধ করেন, তবে আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সাম্প্রতিক ‘অপহরণের’বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই হাস্যকর।
এই অভিযানের পেছনে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদ’ থেকে আমেরিকাকে রক্ষা করার যে দাবি করা হচ্ছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। ভেনেজুয়েলা কখনোই যুক্তরাষ্ট্রে আসা অবৈধ মাদকের (বিশেষ করে ফেন্টানিলের) উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল না। মাদকের বিস্তার রোধে ট্রাম্প আসলে কতটুকু আন্তরিক, তা বোঝা যায় সাবেক হন্ডুরান প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকে তার দেওয়া ‘প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমা’ থেকে, যিনি কি না মার্কিন আদালতেই মাদক পাচারের দায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন।
মার্কিন বিচার বিভাগ এখন নিজেরাই স্বীকার করছে যে, তথাকথিত বিপজ্জনক মাদক কার্টেল ‘কার্টেল দে লস সোলেস’-এর বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। অথচ গত এক বছর ধরে ট্রাম্প প্রশাসন এই কাল্পনিক কার্টেলের নাম জপছিল। সহজ কথায়, এটি ছিল প্রশাসনের সাজানো একটি বানোয়াট প্রোপাগান্ডা। এটি ইরাকে সেই ‘গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র’ খোঁজার গল্পের মতোই অলীক। এর ভয় দেখিয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করা হলেও শেষ পর্যন্ত যার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি।
মাদুরোকে বন্দী করার পেছনে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তাকে সুসংহত করার কোনো বাস্তবসম্মত যুক্তিও নেই। ভেনেজুয়েলা কতটা দুর্বল একটি দেশ, তা মাদুরোকে অতি সহজে আটকের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। দেশটি আমেরিকার শক্তিশালী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘনিষ্ঠ কৌশলগত মিত্রও নয়। সেখানে চীন কোনো সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করছিল না বা ইরানও আমেরিকায় আঘাত হানার জন্য কোনো ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেনি। এমনকি মার্কিন বাণিজ্য পথকে বাধাগ্রস্ত করার মতো কোনো শক্তিশালী নৌবাহিনীও তাদের নেই। সত্যি বলতে, কারাকাস থেকে আসা কোনো ‘ভয়াবহ হুমকির’কথা ভেবে কেউ কখনো রাতে নির্ঘুম কাটায়নি, আর মাদুরো এখন ব্রুকলিনের কারাগারে বন্দি বলে আমাদের নিরাপত্তা রাতারাতি বেড়ে গেছে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই।
এমনকি এই অভিযানের পেছনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কোনো মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল না। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোকে ক্ষমতায় বসানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। বরং তিনি মাদুরোরই এক সহকারীর সাথে আপস করতে আগ্রহী, যার নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা এখনো অনস্বীকার্যভাবে একটি স্বৈরাচারী কাঠামো। সুতরাং, গণতন্ত্রের দোহাই দেওয়াটা এখানে কেবল একটি অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়।
বিপজ্জনক মাদক নির্মূল, নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলা বা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার,যদি এর কোনোটিই মূল উদ্দেশ্য না হয়; তবে কি তেলের কারণেই এই অভিযান? ট্রাম্পের দাবি অন্তত তেমনই। তিনি বারবার বলছেন এটাই আসল কারণ এবং মার্কিন কোম্পানিগুলো সেখানে ঢুকে তেলের দখল নিয়ে আমেরিকাকে আরও মহান করবে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে অন্য কথা। ট্রাম্প নিজের খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে 'আঙ্কেল স্যাম'-এর পকেটে ভেনেজুয়েলার তেল থেকে বড় কোনো মুনাফা আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সম্প্রতি তিনি বড়াই করে বলেছিলেন, ভেনেজুয়েলা আমেরিকাকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল দিতে রাজি হয়েছে। শুনতে এটি বিশাল মনে হলেও বাস্তবে তা আমেরিকায় মাত্র চার দিনের তেল উৎপাদনের সমান। ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন যে, তিনি এই তেল বিক্রির অর্থ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তা ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি পুনর্গঠনে ব্যয় করবেন। কেউ যদি এটি বিশ্বাস করেন, তবে বুঝতে হবে ট্রাম্পের শিকারি মানসিকতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আর যদি সত্যিই সেই অর্থ পাওয়া যায়, তবুও ভেনেজুয়েলার বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের বিশাল খরচের তুলনায় তা হবে ‘সমুদ্রের এক ফোঁটা পানির’ মতো নগণ্য।

এটা ঠিক যে ভেনেজুয়েলায় বিশ্বের বৃহত্তম তেলের মজুদ রয়েছে। কিন্তু সেখানকার তেল মূলত ‘ভারী অপরিশোধিত’। এটি মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা যেমন কঠিন, পরিশোধন করাও তেমনি ব্যয়বহুল। সত্যি বলতে, ভেনেজুয়েলার জরাজীর্ণ অবকাঠামো এবং বিশ্ববাজারে তেলের বর্তমান নিম্নমূল্য বিবেচনায় কোনো বুদ্ধিমান উৎপাদনকারী এই তেল স্পর্শ করার কথা ভাববে না। আর যদি কোনো অলৌকিক ঘটনায় প্রচুর পরিমাণ ভেনেজুয়েলান তেল বিশ্ববাজারে চলে আসে, তবে তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবে। এতে আমেরিকারই ক্ষতি হবে। কারণ দাম কমে যাওয়ায় আমেরিকার অনেক প্রান্তিক ‘শেল অয়েল’ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।
আর ভুলে গেলে চলবে না যে, ট্রাম্প এবং বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো যা-ই ভাবুক না কেন, বর্তমান বিশ্ব ধীর ধীরে হাইড্রোকার্বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শক্তির অন্যান্য উৎসের দিকে ঝুঁকছে। এই পরিবর্তন ভেনেজুয়েলার তেলের মজুদের দামকে দিন দিন আরও কমিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, জলবায়ু পরিবর্তনের কঠোর বাস্তবতায় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ওই তেলের সিংহভাগ মাটির নিচেই রেখে দেওয়া। চীন যখন ভবিষ্যতের পরিবেশবান্ধব শিল্পে আধিপত্য বিস্তারে লেজারের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে এবং বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বাড়াচ্ছে, তখন ট্রাম্প ও তার চারপাশের তথাকথিত ‘কৌশলগত প্রতিভাবানেরা’ গ্রহের জন্য হুমকিস্বরূপ গত শতাব্দীর সেই সেকেলে জ্বালানি নীতি আঁকড়ে ধরছেন।
তাই এই অভিযানের কৌশলগত যৌক্তিকতা নিয়ে আপনার মনে বিভ্রান্তি জাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ এখানে একমাত্র যে কৌশলগত উদ্দেশ্যটি দৃশ্যমান, তা হলো পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি চেষ্টা। যেহেতু ট্রাম্প সবকিছুর ওপর নিজের নামের সিল বসিয়ে নিজের এলাকা বা প্রভাব জাহির করতে পছন্দ করেন, তাই এই ধারণাটিকে এখন ‘ডনরো ডকট্রিন’ হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে। এমনকি সাম্প্রতিক ‘জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল’-এও এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি হয়তো শুনতে এমন এক যুক্তিসঙ্গত ধারণা মনে হতে পারে যা পররাষ্ট্রনীতির বাস্তববাদীরা সমর্থন করবেন, কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে এটিও টিকবে না।

ঐতিহাসিক 'মনরো ডকট্রিন'-এর মূল লক্ষ্য ছিল এটি নিশ্চিত করা যেন পশ্চিম গোলার্ধে অন্য কোনো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তা করতে না হয়। প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এই গোলার্ধ থেকে অন্য সব মহাশক্তিকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং ইতিহাসবিদ সি. ভ্যান উডওয়ার্ডের ভাষায় ‘ফ্রি সিকিউরিটি’র এক অনন্য সুযোগ ভোগ করতে শুরু করে।
তবে ট্রাম্প অ্যান্ড কোম্পানির বর্তমান আলাপচারিতা সেই পুরোনো উদ্দেশ্যকে ধারণ করে না; কারণ বর্তমানে পশ্চিম গোলার্ধে অন্য কোনো মহাশক্তির তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সামরিক উপস্থিতি নেই, আর কেউ তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছে না। বরং ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি’ থেকে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ট্রাম্প প্রশাসন তার প্রতিবেশী দেশগুলোকে আজ্ঞাবহ করতে চায়, যাতে যেকোনো ইস্যুতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলে। মাদুরোর উত্তরসূরিদের তারা এখন সরাসরি এই বার্তাই দিচ্ছে- “আমাদের শর্ত মেনে নাও, নতুবা আমরা অবরোধ জারি রাখব এবং পরিস্থিতি হয়তো আরও ভয়াবহ করে তুলব।” ওয়াশিংটন আশা করছে, তারা আশা করছে যে, ওই অঞ্চলের বাকি দেশগুলোও এই বার্তা পাবে এবং বাধ্য হয়ে অনুগত থাকবে।
বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি এমন সব উদ্যোগে ‘ভেটো’ দেওয়ার অধিকার দাবি করছে, যা ওই রাষ্ট্রগুলোর জন্য কিংবা চীনের মতো দেশের জন্য লাভজনক হতে পারে। ‘জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল’ -এর ভাষ্যমতে, “আমরা এমন একটি গোলার্ধ চাই যা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি অনুপ্রবেশ বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের বিদেশি মালিকানা থেকে মুক্ত থাকবে।” তারা আরও স্পষ্ট করেছে যে, বাইরের কোনো শক্তিকে ‘কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ’ দেওয়া যাবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে গোলার্ধের বাইরের প্রতিযোগীরা এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। ট্রাম্প প্রশাসন বুঝতে পারছে যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো মূলত কম খরচ এবং সহজ শর্তের কারণে চীনের সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু উদার প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ট্রাম্প প্রশাসন হুমকি ও চাপের মুখে ওই দেশগুলোকে এই সহায়তা “প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য” করার নীতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু এই প্রশাসন মূলত একটি স্বার্থলোভী ও অনুদান-বিরোধী মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত, তাই তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের পকেট ভারী করতে চায়; আর এই উদ্দেশ্য হাসিলে তারা উদারতার পরিবর্তে কেবল ভীতির ওপর নির্ভর করছে।
সমস্যা হলো, আমেরিকা যদি প্রতিবেশীদের অর্থনীতিতে এভাবে খবরদারি শুরু করে, তবে সেখানকার যেকোনো বিপর্যয়ের দায় শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের কাঁধেই এসে পড়বে। তারা যদি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে সস্তা ও উন্নত মানের চীনা পণ্য (যেমন: বৈদ্যুতিক গাড়ি) কেনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে, তবে সেখানকার সাধারণ ভোক্তারা চরম অসন্তুষ্ট হবে। একইভাবে, যদি স্থানীয় সরকারগুলোকে চীনা বা বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করা হয় যা কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরি ছিল। তবে সেই অভাব ওয়াশিংটনকেই পূরণ করতে হবে। তা না পারলে লাতিন আমেরিকানদের দারিদ্র্যের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করা হবে। এর সাথে যখন অভিবাসীদের ওপর দোষ চাপানো এবং তাদের গণহারে বিতাড়িত করার প্রশাসনিক জেদ যুক্ত হয়, তখন তা কোনো স্থিতিশীল আধিপত্য তৈরি করে না। বরং এটি হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান মার্কিন-বিদ্বেষ এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার এক চরম প্রেসক্রিপশন।
আমেরিকার অতীতের সফল পররাষ্ট্রনীতিগুলোর সাথে বর্তমান পরিস্থিতির বৈসাদৃশ্য আকাশ-পাতাল। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ইউরোপ ও এশিয়ায় (এমনকি সাবেক শত্রু জার্মানি ও জাপানের সাথেও) অত্যন্ত ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছিল। এর আংশিক কারণ ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আসা একটি অভিন্ন নিরাপত্তা হুমকি। আমেরিকা অত্যন্ত উদারভাবে কাজ করেছিল যাতে তার নতুন অংশীদাররা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে দ্রুত সময়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ট্রাম্পের অভিধানে ‘উদারতা’বা ‘পরোপকার’ বলতে কোনো শব্দ নেই; জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত- “আমার যা আছে তা আমারই, আর তোমার যা আছে তা আলোচনা সাপেক্ষ (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেওয়ার যোগ্য)।”
বন্দুকের মুখে পশ্চিম গোলার্ধ শাসন করার এই নীতি অতীতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার চেয়ে ভালো কোনো ফল বয়ে আনবে না। ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার মনে করেন ইতিহাসের অন্যতম এক ‘অমোঘ বিধান’ বা আয়রন ল হলো, পৃথিবী কেবল ‘শক্তি’ বা ক্ষমতার দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু তিনি ইতিহাসের সেই অমোঘ সত্যটি ভুলে গেছেন যা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আর তা হলো- যেসব নেতা মনে করেন ক্ষমতাই শেষ কথা, তারা অবধারিতভাবে একের পর এক বোকামি করে বসেন।
লেখক: ‘ফরেন পলিসি’ ম্যাগাজিনের কলামিস্ট এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক
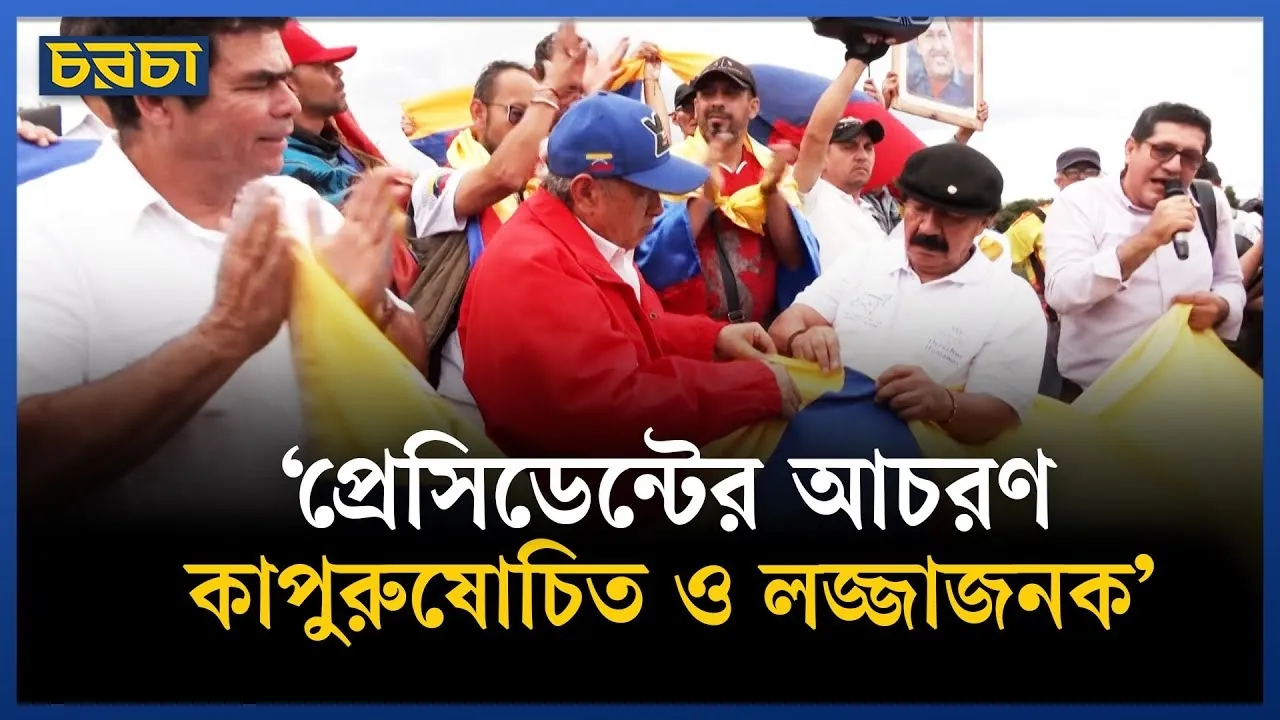 আমেরিকা না ভেনেজুয়েলা, কাকে বেছে নেবে লাতিন আমেরিকা?
আমেরিকা না ভেনেজুয়েলা, কাকে বেছে নেবে লাতিন আমেরিকা? ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য’ ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা
‘অনির্দিষ্টকালের জন্য’ ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা